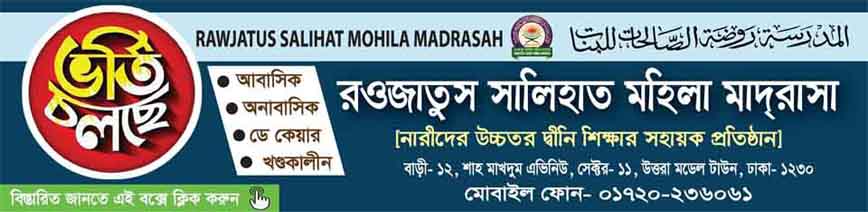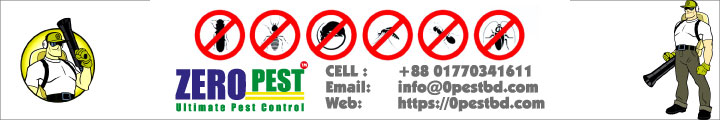।। সরদার সিরাজ ।।
আইএমএফের ৪.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণ (সরকারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমোদন করেছে গত ৩০ জানুয়ারি ও প্রথম কিস্তির ৪৭.৬২ কোটি ডলার দিয়েছে। ২০২৬ সালের মধ্যে ৭ কিস্তিতে সমুদয় অর্থ প্রদেয়) নিয়ে দেশে ব্যাপক আলোচনা চলছে। বিশেষ করে এই ঋণের প্রয়োজনীয়তা ও শর্ত নিয়ে। বিপক্ষেই বেশি বলা হচ্ছে।
কিন্তু সমালোচনা যতই করা হোক না কেন, উক্ত ঋণের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কারণ, বৈদেশিক মুদ্রা মজুদে চরম সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক থেকে গত ৮ মে আকুর বিল পরিশোধের পর রিজার্ভের পরিমাণ ২৩.৩৭ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়, যা গত সাত বছরে সর্বনিম্ন। এ দিয়ে আড়াই মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো যাবে। অথচ, তিন মাসের আমদানি ব্যয়ের রিজার্ভ থাকতে হয়। তাই আগামী জুনেই রিজার্ভ ২৪.৪৬ বিলিয়ন ডলার করার কথা বলেছে আইএমএফ এবং পরবর্তীতে কত করতে হবে তারও শিডিউল দিয়েছে।
দেশের রিজার্ভের প্রধান উৎস রেমিটেন্স ও রফতানি আয় অনেক হ্রাস পাওয়ায় রিজার্ভ সংকটজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। তাও আমদানিতে ব্যাপক লাগাম টানা ও আইএমএফের প্রথম কিস্তি পাওয়ার পরও। ফলে উক্ত ঋণ পাওয়া না গেলে কী হতো, তা সহজেই বোধগম্য। তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘বাংলাদেশ কিছুটা স্বস্তির জন্য আইএমএফের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে’।
গত ২৯ এপ্রিল সংস্থাটির এমডি জর্জিয়েভারের সাথে বৈঠককালে তিনি এ কথা বলেন। অর্থাৎ দেশের বিশেষ প্রয়োজনেই আইএমএফের উক্ত ঋণ নিতে হয়েছে। এছাড়া, ঋণের ক্ষেত্রে সংস্থাটি যে ৩৮টি শর্ত দিয়েছে, তা অযৌক্তিক নয়। শর্তগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে: ভর্তুকি বন্ধ/হ্রাস, ব্যাংকখাতের সংস্কার এবং ব্যাংক ও ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক খাতের হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ, সরকারি ব্যাংকের ঋণ খেলাপির পরিমাণ ১০%-এ নামিয়ে আনা, কর জিডিপির হার বাড়ানো, বিদেশি ঋণের ও তিন মাস অন্তর অন্তর জিডিপি প্রবৃদ্ধির সঠিক তথ্য প্রকাশ, বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ আন্তর্জাতিক মানদন্ডে উন্নীত করা এবং মার্কিন ডলার ও ব্যাংকের সুদ বাজার ভিত্তিক করা।
বর্ণিত শর্তগুলোর ভর্তুকি বন্ধ/হ্রাস ছাড়া কোনটিই দেশের জন্য অযৌক্তিক নয়। তবে, ভর্তুকি বন্ধ/হ্রাস করা হলে সাধারণ মানুষের চরম ক্ষতি হবে। এর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে সর্বত্রই। ইতোমধ্যেই তা হয়েছেও কয়েকবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভর্তুকি কমানোর কারণে। তবুও এ বছরের মধ্যে জ্বালানি খাতের ভর্তুকি বন্ধ করতে রাজী হয়েছে জ্বালানি বিভাগ। উল্লেখ্য যে, জ্বালানি খাতে সরকারের ভুল নীতি ও ব্যাপক দুর্নীতির চরম খেসারত চলছে। এই অবস্থায় ভর্তুকি প্রত্যাহার করা মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে দেখা দেবে!
যা’হোক, জ্বালানির ভর্তুকি ছাড়া আইএমএফের বাকী শর্তগুলোর কোনটিই অযৌক্তিক নয়। কারণ, এসব করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞরা দাবি করে আসছে অনেক দিন থেকে। কিন্তু সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি। নতুবা উক্ত ঋণের কিস্তি দেওয়া বন্ধ হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। তাই আইএমএফের ঋণের প্রয়োজনীয়তা ও শর্ত নিয়েও সমালোচনা করা অবান্তর। বরং শর্ত বাস্তবায়ন হবে কীভাবে এবং তার রেজাল্ট কী হবে সেসব নিয়েই সদুপোদেশ দরকার। নিবন্ধের স্থান সংকুলানের স্বার্থে সব শর্ত ও বাস্তবতা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তাই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করবো।
ব্যাংক খাতের সংস্কার: এটা করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞরা বহুদিন যাবত বলছেন। ব্যাংক কমিশন গঠন করার দাবি জানিয়েছেন অনেকেই। কিন্তু এসব করা হয়নি। ফলে ব্যাংক ও ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক খাতে (বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ৩৫টি) চলছে ব্যাপক তুঘলকি কান্ড! তাই এসব সংস্কার ও ব্যাংক কমিশন গঠন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।
সরকারি ব্যাংকে খেলাপি ঋণের হার ১০% করা: বর্তমানে সরকারি ব্যাংকে খেলাপি ঋণের হার ২০.২৭% (৫৬,৪৬১ কোটি টাকা) ও ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক খাতের গড় খেলাপি ঋণের হার ২৩%। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান তারল্য সংকটে পড়েছে! তবুও বিপুল খেলাপি ঋণ সহজে আদায় হবে না। কারণ, এর অধিকাংশই সরকারি দলের লোকরা নিয়েছে অথবা তাদের তদবিরে ব্যাংক ঋণ দিতে বাধ্য হয়েছে সঠিক কাগজপত্র ছাড়াই। তাই মামলা করেও তেমন লাভ হবে না। উপরন্তু মামলা করলেও তা সহজে নিষ্পত্তি হবে না। এরূপ বহু মামলা পেন্ডিং আছে অনেক দিন থেকে। তাই সরকারি ব্যাংকের ও ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক খাতের খেলাপি ঋণের হার ১০% নামিয়ে আনা কঠিন। তবে, এই ঋণ সংশ্লিষ্টদের কঠোর শাস্তি দিলে ভবিষ্যতে এটা হবে না।
বিদেশি ঋণের সঠিক তথ্য প্রকাশ: বর্তমানে সরকারের দেশি-বিদেশি মোট ঋণের পরিমাণ জিডিপির ৪২.১%,যা ২০১৪ সালে ছিল ২৮. ৭%। সিইআইসির তথ্য মতে, বর্তমানে সরকারের ঋণের পরিমাণ ১৬৭ বিলিয়ন ডলার। তন্মধ্যে বিদেশি ৭১.৯৩ বিলিয়ন ডলার, বাকীটা দেশি। এই বিপুল ঋণ নিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে অনেক মেগা প্রকল্প করা হয়েছে, যার বেশিরভাগই নির্ধারিত সময়ে, অর্থে ও মানে সম্পন্ন হয়নি। ফলে ব্যয় অনেক বেড়েছে। দ্বিতীয়ত: মেগাপ্রকল্পগুলোর মধ্যে পদ্মাসেতু ছাড়া বাকীগুলোর রিটার্ন খুব স্লো। তাই পুঁজি উঠে আসতে বহুদিন লাগবে। তৃতীয়ত: অনেকগুলো প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ আছে কাঁচামালের অভাবে।
এদিকে, বড় ঋণের কিস্তি ও সুদ প্রদান শুরু হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ বাবদ বাজেটে ৮০ হাজার কোটি টাকার অধিক রাখা হয়েছে। এ টাকার পরিমাণ আগামীতে আরো অনেক বাড়বে। এছাড়া, জাতীয় বাজেট বাস্তবায়নের ঋণ তো আছেই। উপরন্তু বেসরকারি খাতেরও বিপুল ঋণ রয়েছে, যার চূড়ান্ত দায় সরকারেরই। তাই কর জিডিপির হার বাড়াতে না পারলে সরকারের ঋণ পরিশোধ করা দূরহ হবে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।
আইএমএফও বলেছে, দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ পেতে (আগামী অক্টোবরে শিডিউল আছে) কর-জিডিপির অনুপাত চলতি অর্থবছরের মধ্যেই ৮.৩% এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৯.৫% করতে হবে, যা সহজতর নয়। তাই সরকারের ঋণের কিস্তি ও সুদ পরিশোধ করতেও নতুন করে ঋণ করতে হবে। তবুও সরকারের ঋণ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। অর্থাৎ দেশ ঋণের ফাঁদে পড়ে গেছে, যা থেকে সহজে নিস্তার নেই!
আরও পড়তে পারেন-
- ঋণ বা ধারকর্য পরিশোধে ইসলামের বিধান
- ইতিহাসে আল্লামা আহমদ শফী
- মেধাবী, আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান শিক্ষক ছাড়া শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব নয়
- ইগো প্রবলেম নিয়ে যত কথা
- সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখতে ইসলামের নির্দেশনা
বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের হিসাব: এ ক্ষেত্রে আইএমএফের শর্ত হচ্ছে, সংস্থাটির বিপিএম-৬ পদ্ধতিতে তথা ব্যবহারযোগ্য হিসাব করতে হবে (ঋণ ও বিনিয়োগকৃত অর্থ হিসাবে ধরা যাবে না, যার পরিমাণ বর্তমানে ৬.৪ বিলিয়ন ডলার। আগে ছিল প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলার)। এটা আইএমএফের নিয়ম, যা বহু দেশ মেনে চলে। তাই আইএমএফের এই শর্ত অযৌক্তিক নয়। তাই রিজার্ভ বাড়াতেই হবে। হুন্ডি, আন্ডার ইনভয়েস, ওভার ইনভয়েস ও অর্থ পাচার বন্ধ, রফতানি বহুমুখীকরণ এবং রপ্তানির যে কয়েক বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিদেশের ব্যাংকে রয়েছে, তা দ্রুত ফিরিয়ে আনতে হবে। তবেই রিজার্ভ বাড়বে।
ডলারের রেট ও ব্যাংকের সুদহার বাজার ভিত্তিক করা: এ ব্যাপারে সরকার রাজি হয়েছে, যা কার্যকর হবে আগামী ১ জুলাই থেকে। ফলে ডলারের রেট অনেক বাড়বে। তাতে পণ্যমূল্যও বাড়বে! ব্যাংকের সুদহার বাজার ভিত্তিক করলে সুদের হার বাড়বে। তাতে ব্যাংকের আমানত ও সঞ্চয় বাড়বে। তবে বেসরকারি বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হবে।
কর জিডিপির হার বৃদ্ধি: বর্তমানে কর জিডিপির হার ৭%, যা বিশ্বের মধ্যে সর্বনি¤œ (নেপালে ২৪.২%, ভারতে প্রায় ২০%, ইউরোপের দেশগুলোতে গড়ে ৪৭%)। তাই সরকার এসডিজি বাস্তবায়নের স্বার্থে ২০২১ সালের মধ্যে কর জিডিপির অনুপাত ১৫% করার টার্গেট করেছিল। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি! অথচ দেশে কয়েক বছর আগেও এ হার প্রায় ১০% ছিল। আইএমএফের প্রতিবেদন-২০২১ মতে, কর জিডিপির হারের ক্ষেত্রে বিশ্বের ১৮৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৬৫তম। এখন এ অবস্থানের অবনমন হয়েছে। অর্থাৎ কর জিডিপির হার কমেছে! চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসেও রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। বাকী সময়েও হবে না। অথচ, সাম্প্রতিককালে দেশে ধনী, অতি ধনী ও ব্যাংকে কোটিপতি একাউন্টধারীর সংখ্যা এবং জিডিপির আকার ব্যাপক বেড়েছে।
উপরন্তু কর বাড়ানোর জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবুও রাজস্ব আয় কমেছে। এ জন্য মানুষের কর প্রদানে অনীহা এবং রাজস্ব অফিসের কিছু লোকের দুর্নীতি ও গাফিলতি দায়ী। কিন্তু রাজস্ব আয় বাড়াতেই হবে। সেটা ব্যক্তি কর, ভ্যাট ও সম্পদ সারচার্জ তথা রাজস্ব আয়ের সব ক্ষেত্রেই। দেশে বর্তমানে ৮২ লাখের বেশি টিআইএনধারী ব্যক্তি রয়েছে। তন্মধ্যে ২৮.৫১ লাখ চলতি অর্থবছরের রিটার্ন দাখিল করেছে। অথচ দেশে কর প্রদানযোগ্য লোকের সংখ্যা প্রায় দুই কোটি। অর্থাৎ সক্ষমতা অনুযায়ী মানুষ কর দেয় না। সরকারি ৩৮টি সেবার ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের সনদ দাখিল করা বাধ্যতামূলক করার পরও এই অবস্থা চলছে। তাই ব্যক্তিকর বাড়ানোর জন্য কঠোর পন্থা নিতে হবে। দেশের বেশিরভাগ ব্যবসায়ী ক্রেতার কাছ থেকে যে ভ্যাট আদায় করে, তা ঠিকমতো জমা দেয় না সরকারের কাছে। যাদের বার্ষিক টার্ন ওভার ৫ কোটি টাকার অধিক, তাদের ভ্যাট নিবন্ধন করতে হয়।
গত আগস্ট পর্যন্ত যার সংখ্যা ছিল ৩,৭১,৯৩৪টি। তন্মধ্যে ২,৯০,৮৯৯টি প্রতিষ্ঠান ভ্যাট রিটার্ন দাখিল করেছে। অথচ, বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির নিবন্ধিত দোকানের সংখ্যা ৩০ লাখ। তাই অর্থনীতিবিদ আহসান মনসুর বলেছেন, গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত ইএফডি দেয়া হলে বছরে ৫ লাখ কোটি টাকার বেশি ভ্যাট আদায় হবে। উল্লেখ্য যে, ভ্যাট সঠিকভাবে আদায়ের লক্ষ্যে এসডিসি মেশিন ছাড়াও ইএফডি পদ্ধতি চালু করা হয়েছে ২০১৯ সালের ২৫ আগস্ট। তখন এ কাজটি এনবিআর করতো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি তেমন না হওয়ায় এটি প্রাইভেট সেক্টরকে দেওয়া হয়েছে গত বছরে জানুয়ারিতে। আগামী পাঁচ বছরে তিন লাখ ইএফডি স্থাপনের টার্গেট রয়েছে। এর ফলাফল কী হবে তা ভবিষ্যৎই জানে।
কিন্তু যেভাবেই হোক, ভ্যাট আদায়ের ক্ষেত্রে শতভাগ সফল হতেই হবে। সে জন্য ভ্যাট নিবন্ধিত সব প্রতিষ্ঠানেই ইএফডি মেশিন স্থাপন করতে হবে দ্রুত। উপরন্তু যদি কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ভ্যাট নিবন্ধনের বাইরে থাকে, তাহলে তাকে ভ্যাট নিবন্ধনের আওতায় আনতে হবে ও ইএফডি মেশিন স্থাপন করতে হবে। সম্পদ সারচার্জ (তিন কোটি টাকার ওপরে সম্পদধারী এবং দুটি গাড়ি ও নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত বাড়ির মালিকদের) সর্বোচ্চ করে তা শতভাগ আদায় করতে হবে। এটা হলে আয় বৈষম্যও কমবে।
রাজস্ব আদায়ের বর্ণিত কাজগুলোর বাস্তবায়ন/তদারকির দায়িত্ব দিতে হবে স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত সংশ্লিষ্ট খাতের লোক ও পুলিশকে। তবেই রাজস্ব আয় বৃদ্ধির স্থায়ী পথ সৃষ্টি ও আদায় দ্বিগুণেরও বেশি হবে। গত ৩ এপ্রিল সিপিডির এক গবেষণা পত্রে বলা হয়েছে, কর ফাঁকি ও কর এড়ানোর ফলে বছরে এনবিআরের ২,৯২,৫০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ক্ষতি হয়। দুর্নীতি, জনবলের অভাব, কম ডিজিটালাইজেশন ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় কম লেনদেনের কারণে এটা হয়। এটা আদায় করা সম্ভব হলে কর-জিডিপি অনুপাত ১৫% হবে। সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন বলেন, ‘আইএমএফ ঋণের যে শর্ত দিয়েছে, তা পূরণ করলেই রাজস্ব খাতের সংকট কেটে যাবে। এছাড়া, ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হবে বাংলাদেশ। তখন বিদেশি সহায়তা কমে যাবে। ফলে অভ্যন্তরীণ খাতের রাজস্ব আয়ের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে’। ইতোমধ্যেই বিদেশি সহায়তা ৩০% কমে গেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২০৪১ সালের মধ্যে কর জিডিপির হার ২৪%-এ উন্নীত করার টার্গেট করা হয়েছে, যা অর্জন করতেই হবে। তবেই নিজস্ব অর্থে কাক্সিক্ষত উন্নতি হবে।
লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট। ইমেইল- sardarsiraj1955@gmail.com
উম্মাহ২৪ডটকম: এমএ