।। ফরিদা আখতার ।।
বিশ্ব আইভিএফ দিবস (২৫ জুলাই) পালন করা হয়, এটা আমার কাছে নতুন তথ্য। আইভিএফ হচ্ছে ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন তথা টেস্ট টিউব পদ্ধতি, যা সন্তান জন্মদানে ‘অক্ষম’ দম্পতিদের সন্তান লাভের জন্য ব্যবহার করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রথমে স্ত্রীর শরীরের বাইরে সন্তান ধারণে সাহায্য করা হয় এবং পরবর্তী গর্ভধারণের পুরো প্রক্রিয়া স্ত্রীর শরীরেই ঘটে। তবে ১০০ জন নারী ঝুঁকি নিয়ে আইভিএফ চিকিৎসা নিলেও মাত্র ৩৫–৪০ জন গর্ভধারণে সফলতা পান। অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ নারী আইভিএফ চিকিৎসার সব ধাপ পেরিয়েও কোনো সন্তানের মুখ দেখেননি।
দৈনিক বণিক বার্তা বিশ্ব আইভিএফ দিবস (২৫ জুলাই, ২০২৩) উপলক্ষ্যে ‘সমাধান’ শীর্ষক চার পৃষ্ঠার একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে। প্রথম পাতাতেই ৪০ শতাংশ সফলতার শিরোনাম। বর্তমানে বাংলাদেশে বন্ধ্যত্বের হার ২০ শতাংশ — এ তথ্য কোনো জরিপ থেকে আসেনি — যারা আইভিএফসেবা দিচ্ছেন তাদেরই হিসাব। জানা গেছে, নিঃসন্তান দম্পতির মধ্যে ৪০ শতাংশ স্ত্রীর, ৪০ শতাংশ স্বামীর, ১০ শতাংশ উভয়ের এবং ১০ শতাংশ অজানা সমস্যার কারণে সন্তান ধারণ করতে পারছেন না ।
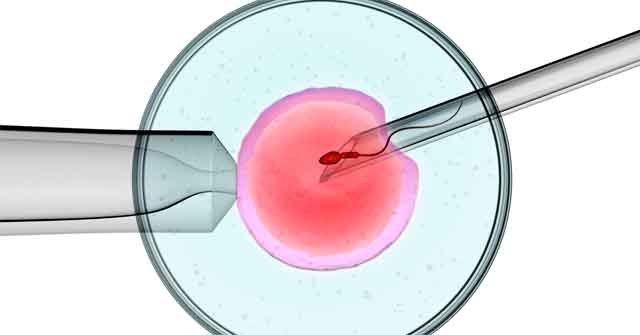
আইভিএফ প্রযুক্তিতে সাধারণত নারীর শরীর থেকে নেওয়া ডিম্বাণুকে ল্যাবে এনে বিশেষ প্রক্রিয়া শেষে শুক্রাণুর সঙ্গে মিশ্রণ ঘটানো হয়। ডিম্বাণু নিষিক্ত হলে আবার সেটাকে নারীর শরীরে জরায়ুতে স্থাপন করা হয়। ছবি- বেবি ইজ লাইফ ডটকম।
এর কারণ কিন্তু কেবল দম্পতির শারীরিক সমস্যা নয় — খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে পরিবেশ দুষণ, খাদ্য উৎপাদনে কীটনাশকের ব্যবহার, ডিটারজেন্টসহ অনেককিছু এতে জড়িয়ে আছে। আর এসব কারণ নিয়ে দম্পতিদের জানার কথাও নয়। এমনকি বিশেষ বিশেষ জন্মনিয়ন্ত্রণও বন্ধ্যত্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে অনেকেই নারীর দেরিতে সন্তান নেওয়ার বিষয়টিকে বড় কারণ হিসেবে দেখেন। নারীর কর্মজীবন কিংবা পড়াশোনার জন্য সন্তান নিতে দেরি হলেও পরে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ কারণটা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক, কিন্তু সমাজে সেটা হয়ে যায় কেবলই নারীর দোষ।
অন্যদিকে পুরুষের সমস্যা একই পরিমাণ থাকলেও সেটা ঠিক মতো পরীক্ষা না করিয়েই স্ত্রীর ওপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং তাকে নানাভাবে, বিশেষ করে মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়। অনেকসময় স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে মেনে নিতে বাধ্য করা হয়, স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়। এ সমস্যাগুলো আইভিএফ-এর মতো প্রযুক্তি কি সমাধান করতে পারবে? অথচ দেখানো হচ্ছে, আইভিএফ একটা ‘সমাধান’, যেখানে ৬০ শতাংশ অর্থাৎ বেশিরভাগ নারীই বিফল হয়ে আরও মানসিক যন্ত্রণার শিকার হচ্ছেন।
সফলতার ছবিগুলোও খুবই হাস্যকর। এখানে ছবি আছে শুধু চিকিৎসকদের, তাদের কোলেই কাপড়ে মোড়ানো নবজাতক শিশু। পুরুষ ও নারী চিকিৎসকেরাই নবজাতক কোলে নিয়ে সফলতা দেখাচ্ছেন — এখানে শিশুটি একটি পণ্য ছাড়া কিছু নয়। তারা যেন ফ্যাক্টরিতে (ল্যাবরেটরি) উৎপাদন করেছেন, এই পণ্যের মালিক তারাই।
ক্রোড়পত্রে কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালের পক্ষ থেকে তাদের আইভিএফসেবা সম্পর্কে প্রচারণামূলক লেখা রয়েছে। এখানে আইভিএফ চিকিৎসা নিতে হলে কত টাকা ব্যয় করতে হবে তার কোনো তথ্য নেই। সম্ভবত হাসপাতালগুলো নিজেদের হিসাবমতো অর্থ নেয়, যা এত খোলামেলা আলোচনায় বলা হয়নি। তবে ইন্টারনেট ঘাঁটলেই গড় খরচের একটি ধারণা পাওয়া যায় — তা হচ্ছে এ লাখ থেকে তিন লাখ টাকা। যারা সফল হয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে এ খরচ পুষিয়ে গেলেও — যারা হননি কিন্তু চিকিৎসার খরচ করে ফেলেছেন — তাদের জন্য এ বোঝা বওয়া কঠিন বৈকি। বিফলতার দায় চিকিৎসক বা হাসপাতাল কেউই নিচ্ছে না, এটা দম্পতিরই পোড়া কপাল। কাজেই সন্তান না হওয়ার সেই গ্লানি তার থেকেই যাচ্ছে।
আইভিএফ প্রযুক্তি এসেছে বাণিজ্যিক স্বার্থেই, নিঃসন্তান দম্পতিদের সান্ত্বনা দিতে নয়। এ প্রযুক্তি প্রথমে এসেছে পশ্চিমা দেশে। প্রথম আইভিএফ শিশু জন্মেছিল ১৯৭৮ সালে যুক্তরাজ্যে। লুইস ব্রাউন নামক ওই শিশুকে নিয়ে গণমাধ্যমে প্রচুর হৈচৈ হয়েছিল। এরপর যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য ধনী দেশের সন্তান জন্মদানে অক্ষম নারীদের জন্য বিশাল ‘সমাধান’ হিসেবে প্রচার করা হয়েছিল এটিকে। নারীদের প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান শুধু প্রযুক্তির মাধ্যমেই করা যাবে — এভাবে প্রচারের মাধ্যমে আইভিএফ-এর ব্যাপক ব্যবসা শুরু হয়ে গিয়েছিল।
আরও পড়তে পারেন-
- প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের বিবাহ্ সম্পর্কে শরয়ী বিধান
- ইসলামের আলোকে নারীর কর্মপরিধি
- সালাম: উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি রক্ষার অন্যতম বাহন
- বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ: বাস্তবতা ও অপপ্রচার
- সকালের ঘুম যেভাবে জীবনের বরকত নষ্ট করে
কিন্তু এরমধ্যেই নারীদের নানা সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে এবং নারীবাদী বিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানীরা আইভিএফ-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করেন। কারণ তারা দেখেছেন, একদিকে উন্নয়নশীল দেশের নারীদের সন্তান বেশি হচ্ছে বলে তাদেরকে নানা ধরনের ক্ষতিকর জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। অন্যদিকে ধনী দেশসমূহে নতুন প্রজনন প্রযুক্তি কিংবা অ্যাসিস্টেড প্রজনন প্রযুক্তির নামে আইভিএফসহ নানা মেডিকেল প্রযুক্তি ব্যবহার করে নারীদের সন্তান ধারনের মেশিন বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে আইভিএফ প্রযুক্তি বিভিন্ন দেশে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু কোথাও এর সফলতার হার ৩০–৪০ শতাংশের বেশি নয়।
আইভিএফ প্রযুক্তির একাধিক ধাপ রয়েছে। সাধারণত নারীর শরীর থেকে নেওয়া ডিম্বাণুকে উপযুক্ত ও নিষিক্ত হওয়ার জন্য অনেক ধরনের ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এরপর সেই ডিম্বাণুকে শরীরের বাইরে এনে ল্যাবে শুক্রাণুর সঙ্গে মিশ্রণ ঘটানো হয়। ডিম্বাণু নিষিক্ত হলে আবার নারীর শরীরে জরায়ুতে স্থাপন করা হয় সেটি। জরায়ুর আস্তরণে ভ্রুণ স্থাপন করলেই কেবল গর্ভধারণ করা হয়। এত ধাপের মধ্যে যেকোনো ধাপেই ব্যর্থতা দেখা যেতে পারে। তবে শুধু বাংলাদেশে নয়, সকল দেশেই আইভিএফ-এর সফলতার হার কম হলেও, ওটুকু সাফল্য দেখিয়েই এ ব্যবসা চলছে।
দেশে আইভিএফ শুরু হয়েছে ২০০১ সাল থেকে। বাংলাদেশে এ প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে উবিনীগ ২০০১ সাল থেকেই গবেষণা করছে। প্রথমে কেবল একটি আইভিএফ কেন্দ্র ছিল। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে বারোটিতে। বড় বড় বেসরকারি হাসপাতাল ব্যবসায়িক সাফল্য দেখেছে এর মাধ্যমে।
তবে আইভিএফ প্রযুক্তি ব্যবহার করার মতো বিশেষজ্ঞ এখনো দেশে নেই। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা কোর্স চালু করা হয়েছে। দেশে আইভিএফ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো নীতিমালাও নেই। গাইনিরোগ বিশেষজ্ঞ না হয়েও মাত্র একটি কোর্স করে কিছু সেন্টার চিকিৎসা দিচ্ছে। কার শরীরে এই প্রযুক্তি দেওয়া যাবে, সেই পরীক্ষা না করেই আইভিএফ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।
২০০০ সালে ‘সেন্টার ফর অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাকশন’ (কেয়ার) নামক প্রথম সেন্টার ডা. পারভিন ফাতিমা শুরু করেছিলেন। তিনি ডেইলি স্টারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে (৯ অক্টোবর, ২০০৩) জানিয়েছিলেন, এ সেবা শুরু করার সময় তার কোনো যন্ত্রপাতি ছিল না, যন্ত্রপাতির ব্যবহার জানে এমন কোনো টেকনিশয়ান ছিল না, এমনকি কোনো ভ্রূণ বিশেষজ্ঞও ছিলেন না। তার শিশু বিশেষজ্ঞ স্বামী কিছু প্রশিক্ষণ নিয়ে ভ্রূণ বিশেষজ্ঞের কাজ করেছিলেন। আইভিএফ-এর এভাবেই যাত্রা শুরু।
এখনো পরিস্থিতির তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। গাইনি বিশেষজ্ঞ না হয়েও অনেকে প্রজনন সেবা দিচ্ছেন। এখানে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কোনো নজরদারি যে নেই তা বোঝাই যায়। কোনো নীতিমালা নেই, তাও পরিষ্কার। অথচ বিশাল ‘সমাধান’ হয়ে হাজির হয়েছে আইভিএফ।
শুরু থেকে আইভিএফ-এ দুই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে: টেস্ট টিউব ও ফ্রোজেন এমব্রায়ো। প্রথম টেস্ট টিউব বেবির জন্ম হয় ২০০১ সালে — একটি নয় একসঙ্গে তিনটি শিশু বা ট্রিপলেট জন্ম নিয়েছিল। হীরা, মণি ও মুক্তার জন্মে খরচ হয়েছিল দুই লাখ টাকা। ষোল বছর পর দম্পতিটি তিনটি সন্তান একসঙ্গে পেলেও তাদের মা বুকের দুধও খাওয়াতে পারেনি। ডাক্তার বলে দিয়েছিল কী করতে হবে। কোথাও আবার চার শিশুও জন্ম নিয়েছে। তবে সব শিশু শেষ পর্যন্ত বাঁচেনি। একসঙ্গে একের অধিক সন্তান পাওয়াটা স্বাভাবিক নয়, বরং টেস্ট টিউব প্রযুক্তি ব্যবহারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবেই এসেছে।
টেস্ট টিউব বেবি প্রযুক্তি নারী ও পুরুষের বন্ধ্যত্বের ওপর ব্যবসারই একটি মাধ্যম। তারা বড় বড় বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করে বন্ধ্যত্ব মোচন করছে আইভিএফ প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন অ্যাসিস্টেড প্রজনন প্রযুক্তির মাধ্যমে। অথচ যেসব কারণে বন্ধ্যত্ব ঘটে, তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। আর অন্যদিকে নারীদের ওপরই সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে পরিবার ও সমাজ নারীকে অত্যাচার করছে। তাদের জন্য আইভিএফ কোন সমাধান দিচ্ছে? আইভিএফ নিলেও তারা ৬০ শতাংশের মধ্যে পড়বে না, তারই-বা কি কোনো গ্যারান্টি আছে?
এই প্রযুক্তি ব্যবহারে নীতিমালা ও নজরদারি দরকার। নইলে অনেক নারীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে যেতে পারে।
লেখক: প্রাবন্ধিক ও মানবাধিকার কর্মী।
উম্মাহ২৪ডটকম: এসএ










