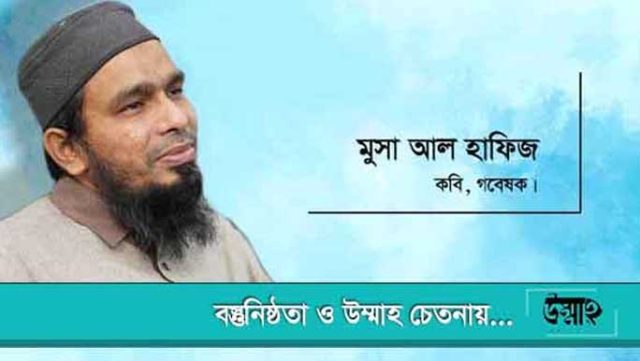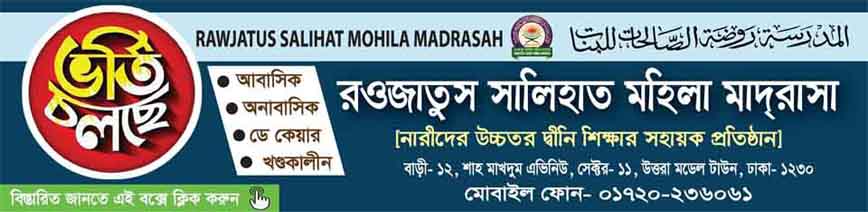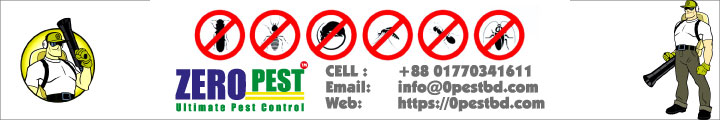।। মুসা আল হাফিজ ।।
ঈশ্বর সম্বন্ধে পশ্চিমা চিন্তাধারার প্রধান দিক নাস্তিকতা নয়। এরিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.) থেকে নিয়ে স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭) হয়ে আজ অবধি চলমান ঈশ্বরভাবনার অধিকাংশই আস্তিকতার বিস্তৃত রূপের মধ্যে পড়ে। এ আস্তিকতা স্বীকার করে যে, একজন ঈশ্বর আছেন। যিনি মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। তিনি সীমাহীন আপন জ্ঞানে, শক্তিতে ও সর্বব্যাপিতায়। তিনি নৈতিক পরিপূর্ণতার স্বয়ংসম্পূর্ণ ধারক। যদিও খ্রি.পূর্ব পঞ্চম শতকের কবি ও দার্শনিক মেলোসের দিয়াগোরাস থেকে নিয়ে হিউম (১৭১১-১৭৭৬) এবং নিটশের (১৮৪৪-১৯০০) মতো অনেকেই ঈশ্বর বিশ্বাসের সমালোচনা করেছিলেন। এ ধারার সা¤প্রতিক পুরোধা হচ্ছেন ভিক্টর জে স্টেংগার (১৯৪৫-২০১৪) ক্রিস্টোফার হিচেন্স (১৯৪৯-২০১১) স্যাম হ্যারিস ( ১৯৬৭-) ও রিচার্ড ডকিন্সগণ (১৯৪১-)। মধ্যখানে সেন্ট অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০ খ্রি.), সেন্ট আনসেল্ম (১০৩৩/৩৪-১১০৯), টমাস অ্যাকুইনাসের (১২২৫-১২৭৪) মতো ভাষ্যগুলো ঈশ্বরবিশ্বাসকে দার্শনিক সত্য হিসেবে প্রমাণের জোরালো চেষ্টা করে।
উইলিয়াম পেলে (১৭৪৩-১৮০৫) কিয়ের্কেগার্ড (১৮১৩-১৮৫৫) হয়ে এ কালের গ্যাব্রিয়েল ভানিয়ান (১৯২৭-২০১২), চার্লস উইনকুইস্ট (১৯৪৪-২০০২), মার্ক সি টেইলর (১৯৪৫-) গিয়ান্নি ভাট্টিমো (১৯৩৬-), জেমস কে এ স্মিথ (১৯৭০-), পিটার রুলিংস (১৯৭৩-) অবধি সেই ধারা চলমান। খ্রিষ্টধর্ম ঈশ্বরের যে ধারণা দেয়, এর সাথে গভীর ও গঠনমূলক বিশ্লেষণে অবতীর্ণ হন এমনকি লাইবনিজ (১৬৪৬-১৭১৬) ও হেগেল (১৭৭০-১৮৩১)। প্লেটো (৪২৭-খ্রিষ্টপূর্ব ৩৪৭) এরিস্টটল বা প্লোটিনাসের (২০৪/৫-২৭০ খ্রি.) ভাবধারা পশ্চিমা খোদাভাবনার সাথে ও সুরে অমোচনীয় জন্মদাগ রেখেছে। সে উত্তরাধিকার স্বীকার করেও তা ইবরাহিমী ধর্মসমূহের মাধ্যমে নিবিড়ভাবে প্রভাবিত। যার কেন্দ্রে আছে ইহুদি ও খ্রিষ্ট্রীয় বিশ্বাস। এর পাশাপাশি ইসলামী কালাম দর্শনের খোদাতত্ত্ব পশ্চিমা দর্শনের ঈশ্বর অন্বেষাকে প্রবল অর্থে প্রভাবিত করেছে। পশ্চিমা দর্শন অনুসন্ধান করেছে ঐশ্বরিক গুণাবলির প্রকৃতি, সেগুলো জানার প্রক্রিয়া, সেই জ্ঞানের সাথে যোগাযোগের উপায়, ঈশ্বর বিশ্বাসের সাথে যুক্ত জ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যার সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়। তার অন্বেষার মধ্যে ছিল ঐশ্বরিক কার্যকারণের প্রকৃতি, ঈশ্বর এবং ঐশ্বরিক ব্যাপারের সম্পর্ক, মানুষের ইচ্ছা ও অবস্থান ইত্যাদি।
প্রাচীন দার্শনিক জেনোফেনিস (৫৭০- ৪৭৮ খ্রিষ্টপূর্ব) বহু ঈশ্বরবাদের সমালোচনা করেন। মনুষ্যরূপী দেবদেবীকে প্রত্যাখ্যান করেন। তার মতে, ঈশ্বরের আকৃতির কল্পনা করাও অন্যায়। আকৃতি কল্পনার মধ্য দিয়ে মূলত ঈশ্বরের ধারণাকে বিকৃত করা হয়। মানুষ যে আকৃতিই তাকে দেয়, সেটা তাদের অভ্যস্ত সীমাবদ্ধতার ফসল। ষাঁড়েরা যদি আঁকতে পারত, তাহলে ঈশ্বরের ছবি তারা নিজেদের মতো আঁকত। মরণশীল জীবের সাথে বুদ্ধি বা আকৃতির দিক থেকে এই ঈশ্বরের কোনো তুলনা হয় না। জাগতিক কোনো কিছুর আদলে তাকে কল্পনা করা চলে না। ঈশ্বরকে ভক্তি করা মনের ব্যাপার। এ জন্য ঈশ্বরকে আকৃতি দিয়ে সামনে রাখার কোনো দরকার নেই। তিনি সবসময় একই স্থানে বিরাজ করেন। তিনি গতিশীল নন; একবার এখানে, একবার ওখানে যাতায়াত করা তার মানায় না। তার মতে, দেবদেবীর জন্ম নেই, তাদের জন্মবৃত্তান্ত একান্তই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সর্বেশ্বরবাদী ছিলেন তিনি। ঈশ্বর বলতে তিনি বুঝিয়েছেন এক অনন্ত বিকারহীন প্রকৃতিজগতকে। তিনি এমন কোনো সত্তা নন, সার্বভৌম বা পালকসত্তার মতো ঐশ্বরিক গুণাবলি যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
হেরাকিটাস (আ. ৫৩৫ আ. ৪৭৫ খ্রি.পূ.) প্রকৃতিকে অনুভব করেছিলেন এক সমগ্ররূপে। বিশ্বজগতকে তিনি মনে করতেন সদা পরিবর্তনশীল এবং নিত্যনতুন পরিণামের অধীন। গতি ও পরিবর্তনই বিশ্বের ধর্ম। সব গতি ও পরিবর্তনের একক হলেন ঈশ্বর। এই একককে আগুন বলা যায়, প্রজ্ঞাও বলা যায়। ঈশ্বর এক, এক সার্বিক বিচারবুদ্ধি, সার্বিক এক নীতি। যে বুদ্ধি বা নীতি সব জিনিসের মধ্যে অন্তর্নিহিত থেকে সব জিনিসকে করে রাখছে ঐক্যবদ্ধ। এক সার্বিক নিয়মানুসারে যা নিয়ন্ত্রণ করছে বিশ্বের অবিরত পরিবর্তনকে। তার ঈশ্বরতত্ত্বের মূল বিষয় তিনটি। সেগুলো হলো ঐক্য, আদি-অন্তহীন পরিবর্তন এবং জগৎ-শৃঙ্খলার নিয়মের অলঙ্ঘনীয়তা। তিনিও ছিলেন সর্বেশ্বরবাদী। তবে জেনোফানিসের মতো নন। জোনোর ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের সাথে বিশ্বজগতের সম্পর্ক অস্পষ্ট। হেরাকিটাসের ব্যাখ্যায় ঈশ্বর জগতের অন্তর্র্বর্তী এক আত্মা। নিজ থেকেই তিনি গড়েছেন প্রকৃতি, ইতিহাস, ধর্ম, আইন এবং নৈতিকতা।
পারমেনাইডস ঐশ্বরিক সত্যকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নয়, পেতে চেয়েছিলেন যুক্তির দ্বারা। মহাবিশ্বের যৌক্তিক ব্যাখ্যার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে চেয়েছিলেন তিনি। সে জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধির সত্যতার সরাসরি বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। তার মতে দেখা, শ্রবণ বা অনুভূতি কোনো কিছুকে নিশ্চিত করে না, তবে কেবল বিশ্বাস এবং মতামত দেয়। অন নেচার কাব্যে তিনি কথা বলেন পরম সত্তাকে নিয়ে, যার অস্তিত্বকে তিনি অকল্পনীয় বলে ঘোষণা করেছিলেন। এ ধারা যুক্তির মধ্যে পরমকে খুঁজতে গিয়ে শেষ অবধি যুক্তিকেই পরম হিসেবে ভাবার পথ উন্মুক্ত করে।
পিথাগোরাস (৫৭০-৪৯৫ খ্রি.পূ.) ও তার অনুসারীরা শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন গণিতে। একে তারা চূড়ান্ত সত্তা হিসাবে ধর্মীয় তাৎপর্য দেন। স্টোয়িকরা ঐশ্বরিক কারণের সাথে আদেশ চিহ্নিত করেছিলেন। স্টোয়িকদের মতে, জগৎ ও ঈশ্বরে কোনো প্রভেদ নেই। সমুদ্রের সাথে জলকণার যে সম্পর্ক, অনন্ত বিশ্বের সাথে মানুষেরও সেই একই সম্বন্ধ। মানবদেহ বিশ্ব উপাদানেরই অংশ এবং মানবাত্মা বিশ্বাত্মারই শ্বাস-প্রশ্বাস। এসবের মধ্যেই ঈশ্বর ছড়িয়ে আছেন। যেভাবে সারা দেহে ছড়িয়ে থাকে আত্মা। প্রজ্ঞা এবং প্রকৃতি সমান্তরাল। অতএব প্রজ্ঞাধারী বা দার্শনিক মাত্রই সত্যের পরিপূর্ণ শৃঙ্খলার অধিকারী। দার্শনিক ঈশ্বরের মতোই স্বাধীন।
প্লেটো ছিলেন এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। সে ঈশ্বর অতীন্দ্রিয়-সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে নিখুঁত সত্তা। চিরন্তন রূপ ব্যবহার করে মহাবিশ্বকে তিনি তৈরি করেন। ফলে মহাবিশ্বও চিরন্তন এবং অসৃষ্ট। তিনি একে দিয়েছেন আদেশ ও উদ্দেশ্য। তবে এই মহাবিশ্ব সীমাবদ্ধ হয়েছে উপাদানের অভ্যন্তরীণ অপূর্ণতার কারণে। এই অপূর্ণতা বিদ্যমান আছে মহাবিশ্বে। মহাবিশ্বের সব কারণের কারণ হলেন ঈশ্বর। যেহেতু গ্রহের গতি অভিন্ন এবং বৃত্তাকার, আর এই গতিই যেহেতু কারণের গতি, তাই একটি গ্রহকে অবশ্যই একটি যুক্তিবাদী আত্মা দ্বারা চালিত হতে হবে। কেননা সব কিছুর জন্য প্রয়োজন একটি স্ব-চালিত প্রবর্তক। এখানে এসে প্লেটো একেশ্বরবাদের দিকে ঝোঁকেন। তার মতে, চালক আত্মাগুলোকে দেবতা বা ঈশ্বর বলা যেতে পারে। মন্দের জন্য শাস্তির রচয়িতা ঈশ্বর। কারণ এ শাস্তি দুষ্টের উপকার করে।কিন্তু এখানে যা কিছু খারাপ, এর নির্মাতা বা চালক ঈশ্বর নন।
ঈশ্বরের ভালোত্ব পরিবর্তনযোগ্য নয়। জগতে যা কিছু আছে তার সবই বিশ্বাত্মারই খণ্ডিত প্রকাশ। আত্মা আধ্যাত্মিক দ্রব্য। সে দেহাতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য বুদ্ধিগম্য পদার্থ। এই আত্মাই মানবচেতনার মূল কারণ। আত্মা এমন একটি জিনিস যা কোনো দেহ ছাড়াই পৃথকভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। দেহহীন অস্তিত্ব হলো আত্মার একটি আদর্শ অবস্থা, যখন আত্মা দেহের বন্দিশালা থেকে মুক্ত হয়ে চিরকালের জন্য শাশ্বত ও পরমসত্তায় বাস করতে পারে। আত্মা তাই অবিনশ্বর। আর ঈশ্বর হলেন আত্মা। তার কাজে কোনো নিত্যনবায়ন নেই।
এরিস্টটলের ঈশ্বর হলেন বিশ্বের বিন্যস্ত সব আকারের সর্বোচ্চ, শুদ্ধতম ও বাস্তব আকার। আর যত অস্তিত্ব আছে, সবাই কমবেশি অবাস্তব। আকারহীন উপাদান পুরোপুরি অবাস্তব। যেসব উপাদানে বাস্তবতা আছে, তাতে বাস্তবতার মাত্রা কম থেকে উপরের দিকে যায়। সর্বোচ্চ ও সর্বনিরক্ষেপ বাস্তবতাই হলেন ঈশ্বর।
ঈশ্বর নিজেই আকার, নিমিত্ত ও পরিণতি। আকারগত কারণ হিসেবে ঈশ্বর হলেন আইডিয়া; ধারণা, চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তা। নিমিত্ত কারণ হিসেবে তিনি হলেন সব গতি ও সমীচীনতার অন্তিম কারণ। কেননা তিনি নিজে প্রবর্তিত নন। সব প্রবর্তনের প্রথম প্রবর্তক তিনি। এই প্রথমতা কালগত অর্থে নন। কারণ এরিস্টটলের মতে, অনন্তকাল ধরে জগত অস্তিত্ববান। তার ঈশ্বর আদিকারণ নিত্য গতির নিত্য উৎস হিসেবে। পরিণতিগত কারণ হিসেবে তিনি পরম উদ্দেশ্য। সব লক্ষ্যের লক্ষ্য তিনি। তিনি যেহেতু পরম লক্ষ্য, তাই তিনি পরম পূর্ণতা। পরম লক্ষ্যের নিজ ছাড়া অন্য কোনো লক্ষ্য থাকতে পারে না। তাই পরম লক্ষ্যের গতির কথা বলা যেতে পারে না। তিনি গতিহীন।
তার ঈশ্বর হবেন পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত। তিনি অব্যক্ত হবেন না। তিনি পরিবর্তন ঘটান। কিন্তু নিজে অপরিবর্তিত থাকেন। তিনি যেহেতু পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত, তাই তিনি উপাদানহীন। যদি তিনি উপাদানযুক্ত হতেন, তাহলে পরিবর্তিত হওয়ার আশঙ্কা আসে, এক উপাদানের ওপর অন্য উপাদানের ক্রিয়ার প্রশ্ন আসে। নিখুঁত হিসাবে তিনি অপরিবর্তনীয়। কারণ তিনি যতটা নিখুঁত আছেন, তার চেয়ে বেশি নিখুঁত হতে পারেন না। সময় যেহেতু অনন্ত, ঈশ্বরকেও অনন্ত হতে হবে। তাকে অনন্ত হতে হলে অবশ্যই জড়বস্তু হতে হবে। কারণ শুধু জড় বস্তুই পরিবর্তন থেকে মুক্ত। আর একটি জড়সত্তা হিসাবে ঈশ্বর মহাশূন্যে প্রসারিত নন। এরিস্টটল ঈশ্বরকে অপ্রবর্তিত প্রবর্তক হিসেবে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেন। কিন্তু তিনি কি এক না বহু? কখনো তাকে এক হিসেবে তিনি দেখান, কখনো দেখান বহু হিসেবে।
উপাদানহীন হওয়ায় কোনো কাজ করতে পারেন না এরিস্টটলের ঈশ্বর। তার কাজ আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক। সে কাজ মূলত চিন্তন। তার চিন্তা তিনি নিজেই। তিনিই চিন্তা, তিনিই চিন্তার কর্তা, তিনিই চিন্তার বিষয়। তিনি চিন্তার চিন্তা। নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই তিনি ভাবতে পারেন না। ঈশ্বর শুধু নিজেকে জানেন, আর কাউকে নয়। জগত সম্পর্কে তিনি অবগত নন। জগতের জ্ঞানে যেমন তিনি নেই, তেমনি তিনি কর্ম ও ঘটনাচক্রকে পরিচালনা করছেন না। এসব কিছুর সাথে তার কোনো যোগ নেই। তিনি কোনো কিছুকেই চালাচ্ছেন না। তদুপরি তিনি অবিচল এক চালক।
আরও পড়তে পারেন-
- প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের বিবাহ্ সম্পর্কে শরয়ী বিধান
- ইসলামের আলোকে নারীর কর্মপরিধি
- সালাম: উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি রক্ষার অন্যতম বাহন
- বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ: বাস্তবতা ও অপপ্রচার
- সকালের ঘুম যেভাবে জীবনের বরকত নষ্ট করে
নব্য প্লেটোবাদের জনক মিসরীয় দার্শনিক প্লটিনাসের ঈশ্বর এক অনন্ত সত্তা। যে সত্তার প্লাবন হচ্ছে বিশ্বজগত। যত অস্তিত্ব আছে এখানে, যত বিরোধ আর বৈপরীত্য আছে এই নিখিলে, যত রূপ আর মাত্রা আছে দেহ-মনে, যত উপাদান আছে জগতজুড়ে, সব কিছুর উৎস হলেন ঈশ্বর। তিনি একক, বহুত্বের ঊর্ধ্বে। তার একত্বের আওতায় আছে সব কিছু। যেভাবে সব কিছুর জন্ম হয়েছে তার থেকে। ঈশ্বর কী, তা আমরা বলতে পারি না। কারণ যে গুণই তার ওপর আমরা আরোপ করি, তা কেবল ছোট করে তাকে। আমরা কেবল বলতে পারি, তিনি কী নন। তিনি কি স্রষ্টা? না, স্রষ্টা হতে হলে দরকার চেতনা ও ইচ্ছা। এগুলো তার মধ্যে আছে বলা হলে তাকে ছোট করা হয়। জগতকে তিনি সৃষ্টি করেননি। যদিও জগত জন্ম নিয়েছে তার থেকে। আগুন থেকে যেভাবে তাপের উদ্ভব হয়, ঈশ্বর থেকেও তেমনি উদ্ভব হয়েছে এই জগতের। উদ্ভব হওয়ার এ ঘটনা ঘটেছে প্রধান তিন স্তরে। প্রথমত, বিশুদ্ধ ভাবনা ও বুদ্ধি। দ্বিতীয়ত, আত্মা। তৃতীয়ত, জড়। প্রথম স্তরে ঈশ্বর চিন্তাকে চিন্তা করেন। বিশুদ্ধ যথার্থতাকে ধ্যান করেন। ভাবনামগ্ন মন আর মনের ভাবনায় পার্থক্য থাকে না। তিনি নিজের সেই ভাবনাকে ভাবেন, যা তারই সারধর্ম থেকে জন্ম নিয়েছে। এ চিন্তা এক ধারণা থেকে অন্য ধারণায় বা সিদ্ধান্তে যায় না। এ এক স্থির ভাবনা, যাতে স্থির প্রত্যয়সমূহকে সমবেতভাবে ধ্যান করা হয়। জগতে বস্তুর সংখ্যা যত, প্রত্যয়ের পরিমাণ তত। সব প্রত্যয়ের সমবেত কেন্দ্র ঈশ্বরের একত্বে প্রতিফলিত হয়। যেসব বস্তু জগতে আছে, প্রত্যেকের জন্য ঈশ্বরের মনে রয়েছে একেক প্রত্যয়। প্রত্যয়গুলো নিজেই মডেল এবং ক্রিয়াশীল। উদ্ভবের প্রতিটি স্তরে তারা হয়ে ওঠে পরবর্তী স্তরের নিমিত্ত বা কারণ। অতএব চিন্তা এবং প্রত্যয় হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র। ফলে এই স্তরে ঈশ্বরের সত্তা বিভক্ত হয়ে যায় দুই ভাগে। এক ভাগ বুদ্ধি, আরেক ভাগ প্রত্যয়।
উদ্ভবের দ্বিতীয় স্তরে বিশুদ্ধ চিন্তা বা বুদ্ধি থেকে নির্গত হয় আত্মা। স্বভাবের বিচারে আত্মা যদিও বুদ্ধির মতোই, তবুও সে বুদ্ধির চেয়ে দুর্বল। সে মূলত বুদ্ধির প্রতিবিম্ব। জড় জগতের স্বভাব যেমন তার মধ্যে আছে, তেমনি আছে প্রত্যয় জগতের স্বভাব। তার মধ্যে প্রত্যয় জগত রয়েছে। আবার সে নিজেও এক বিশুদ্ধ প্রত্যয়। সে অতীন্দ্রিয় জগতের অধিবাসী। সে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত, বস্তুত সে বিশ্বাত্মা। উদ্ভবের তৃতীয় স্তরে বিশ্বাত্মা থেকে বিকীর্ণ হয় দ্বিতীয় আত্মা, যার নাম প্রকৃতি। বিশ্বাত্মা ও প্রকৃতি থেকে জন্ম নেয় অন্য সব আত্মা। বিশ্বাত্মার সৃজনীশক্তির নাম প্রকৃতি। ভৌত পদার্থের জন্ম হয় আত্মার নিচের স্তরে ঐশ্বরিক শক্তির বিকিরণের ফলে। এ কারণে ঐশ্বরিক শক্তির নিম্নতম প্রকাশ হলো ভৌতপদার্থ। আত্মা তার শক্তি প্রয়োগ করতে পারে না কোনো উপল ছাড়া। তাই শক্তিপ্রয়োগের জন্য সে সৃষ্টি করে জড় পদার্থ। এই জড়জগত হলো বিকিরণের তৃতীয় স্তর, নিম্নতম স্তর। জড় পদার্থ হচ্ছে অন্ধকার এলাকা। অন্ধকারকে যেমন দেখা যায় না, তেমনি জড়ের স্বরূপও স্থির করা যায় না। প্লেটোর ভাষায় জড় হচ্ছে অসত্তা।
তাহলে ঈশ্বর থেকে উদ্ভবের যে স্তরগুলো দেখা যাচ্ছে, তার একটি সর্বোচ্চ স্তর, আরেকটি কম বাস্তব। শেষেরটি বস্তু, প্লটিনাসের ভাষায় যার কোনো রূপই নেই, ইতিবাচক অস্তিত্ব নেই। বিশ্বজগতের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্কের মূলে আছে এই উদ্ভব। তারপর ঈশ্বর নিজের মধ্যে এবং নিজেকে নিয়েই আছেন। নিজেই নিজেকে ভাবছেন, বুঝছেন। এ ঈশ্বর বুদ্ধির অগম্য। কেবল অনুভূতি ও প্রেম দিয়ে তাকে বোঝা যায়।
শেষ অবধি প্লটিনাসের ঈশ্বর প্লেটোর ঈশ্বর থেকে খুব একটা আলাদা হন না। প্রথম উদ্ভবে এ ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। এরপর জগতের কোনো সমস্যা সমাধানে তার ভূমিকা নেই। এরিস্টটলের ঈশ্বরও শাসক বটে, কিন্তু শাসন করেন না। শক্তিমান বটে, কিন্তু সমাধান দেন না কোনো সমস্যার। হেরাকিটাস-পিতাগোরাস প্রমুখের ঈশ্বর তো আরো বেশি দূরান্বয়ী, প্রভাবহীন!
ঈশ্বর-অন্বেষায় গ্রিক দৃষ্টিকোণ নানা অস্পষ্টতা, পরস্পরবিরোধ ও অস্বচ্ছতাকে সঙ্গী করেই বিকশিত হয়েছে। পশ্চিমা খোদাদর্শন এ উত্তরাধিকারকে পরবর্তীতে নানাভাবে বহন করেছে। তার ঈশ্বর চিন্তার শরীর ও মনে রয়ে গেছে গ্রিক রক্ত-জল।
লেখক: কবি, গবেষক।
ই-মেল: 71.alhafij@gmail.com
উম্মাহ২৪ডটকম: এমএ