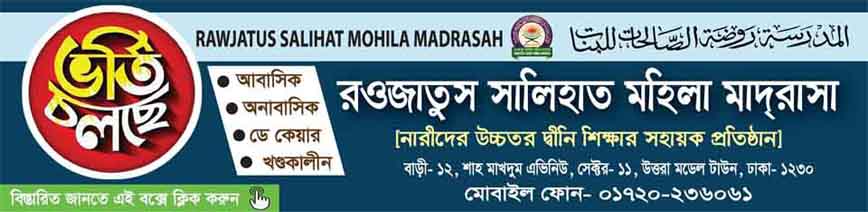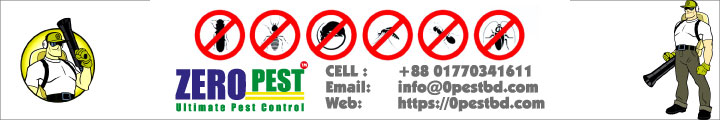।। অরুন্ধতী রায় ।।
আমি ভাবি, সাহস আসলে কী? সাহসের উৎপত্তি কোথা থেকে। নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছিলেন, ‘সাহস মানে ভয় না থাকা নয়, বরং ভয়কে জয় করা।’ এই কথাকে চাইলে অনেক বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কিংবা সাহসের আরও নানা সংজ্ঞা নিয়েও ভাবা যায়। কিন্তু আমি সাহস বলতে বুঝি, একটা পাখিকে পাখি বলতে পারা কিংবা একটা সমুদ্রকে সমুদ্র। আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় সংকট সম্ভবত একটা বিষয় যেমন তেমনটা বলতে না পারা। যেহেতু এই সময়ে এসে আগুনের ওপর বসে সহজ-সরল কথাগুলো খুব বেশি মানুষ বলতে পারেন না, তাই অল্প যে কজন মানুষ বলতে পারেন, তাদের আমরা সাহসী মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করি।
আজকের প্রেক্ষাপটে সাহসকে আমি রাজনৈতিক প্রতিরোধের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করি। কিছু সাহসী মানুষ আছেন বলেই আমরা এখনো অন্ধকারে জোনাকির আলো দেখতে পারি, তার পিছু পিছু হাঁটতে পারি। হয়তো খুব বেশি মানুষ সেখানে থাকেন না। হয়তো শিরদাঁড়া খাড়া করে একজন মানুষই শুধু দাঁড়িয়ে থাকেন নীরবে, কিন্তু যিনি দাঁড়িয়ে থাকেন, তিনিই ওডিসিওস কিংবা জোয়ান অব আর্ক। প্রতীকী অর্থে আমাদের সময়ের সেই জোয়ান অব আর্ক হলেন অরুন্ধতী রায়। ভিড়ের মধ্যেও যার একাকী দাঁড়িয়ে থাকার সাহস ও দৃঢ় মনোবল আছে।
ভিড়ের মধ্যে আলাদা কিন্তু হওয়া মোটেই সহজ নয়। সেই ভিড় যদি আবার মবের মতো কিছু হয়, তবে তো আরও কঠিন। অরুন্ধতী রায় মূলত সেই ভিড় বা মবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই জারি রেখেছেন। যখন যেখানে যে কথা বলার দরকার ছিল, নির্দ্বিধায় বলছেন। অরুন্ধতীর এই সাহস অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দর।
সাহসী অরুন্ধতীর কথা আমরা কমবেশি সবাই জানি। যদিও আমার আগ্রহের কেন্দ্রে তার সৃষ্টিশীল জগৎ। তার বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই দাঁড়িয়েই আছে সাহস এবং সত্যি কথা বলার ওপর। এমনকি রামচন্দ্র গুহের মতো ইতিহাসবিদের সঙ্গে বিতর্কের সময়ও নিজের জায়গা থেকে একচুল সরে আসেননি। অরুন্ধতীকে ক্রিটিক করে রামচন্দ্র যখন ‘আত্মপ্রচারসর্বস্ব’ বলে অভিযোগের তির দাগেন, তখন সে অভিযোগের জবাবে অরুন্ধতী যা বলেন, সেখানে আমরা পাই একজন তুমুল সৃষ্টিশীল অরুন্ধতীকে।
এক সাক্ষাৎকারে ‘আত্মপ্রচারসর্বস্বতার’র অভিযোগ খণ্ডন করে অরুন্ধতী বলেন, ‘একজন চিত্রকর, লেখক, গায়ক তথা সৃষ্টিশীল মানুষের অন্তর্দৃষ্টি, আত্মচিন্তা এবং সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে নানাভাবে স্থাপন করে দেখার নিরীক্ষা, অনেক সময় এটাই শিল্প। উত্তম পুরুষের ব্যবহার লেখকদের বহুল প্রচলিত চর্চা। এই চর্চাকে আত্মপ্রচারের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া শুধু নিষ্ঠুরতাই নয়, সস্তা চালবাজি।’ বুদ্ধিজীবিতা কিংবা রাজনৈতিক ভাবাদর্শের সঙ্গে সৃষ্টিশীলতার সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বকে যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন অরুন্ধতী।
বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে শিল্পীর সৃষ্টিশীলতা কিংবা নীরিক্ষাকে নেতিবাচকভাবে দেখার যে স্থূল চর্চা, তার বিরুদ্ধে অরুন্ধতীর অবস্থান স্পষ্ট। আরেক জায়গায় অরুন্ধতী বলছেন, ‘একজন ফিকশন লেখকের সবচেয়ে অপমানজনক হচ্ছে মৌলিক কাজ না করে এমন কিছুতে নিজেকে জড়ানো, যা নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক জ্ঞানী, নিবেদিত, দক্ষ লোকজন কাজ করে ফেলেছেন।’
নিরীক্ষা ও সৃষ্টিশীলতার পক্ষে নিজের অবস্থান ব্যক্ত করার পর অবশ্য নিজের ব্যক্তিগত পছন্দটাও স্পষ্ট করতে ভোলেননি অরুন্ধতী, ‘কিন্তু নিজেকে অপমানটুকু করার জন্য আমি প্রস্তুত আছি। কারণ, এটা এমন এক সময়, চুপ থাকার পক্ষে যুক্তি দেখানোর কোনো সুযোগ নেই।’
এই হলেন অরুন্ধতী! অকপট থাকতে পারার এই শক্তিই অনন্য করেছে তাকে। এই প্রসঙ্গে অবশ্য আরেকজন লেখকের কথা না বলে পারছি না। উরুগুয়ের তমুল রাজনৈতিক লেখক এদুয়ার্দো গালিয়ানো। লেখককে সরাসরি রাজনৈতিক কণ্ঠ হওয়ার দায় থেকে গালিয়ানো মুক্তি দিচ্ছেন এভাবে, ‘আমি মনে করি না, লেখকদের রাজনৈতিক হতেই হবে। আমি মনে করি, লেখককে সৎ হতে হবে, যা তারা করছে, সে বিষয়ে সৎ। নিজেকে তারা বিক্রি করবে না। তারা যেন নিজেদের কাউকে কেনার অনুমতি না দেয়। নিজেদের শ্রদ্ধা করতে হবে তাদের। মানুষ হিসেবে এবং পেশাদার লেখক হিসেবে নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখতে হবে তাদের। তারা যা বলতে চায়, তা যেন বলতে পারে। শব্দগুলো খাঁটি হতে হবে, আর তা যেন সরাসরি হৃদয় থেকে আসে, না হলেই কৃত্রিম হয়ে যাবে। যখনই তুমি রাজনৈতিক হওয়ার আদেশ জারি করবে, অমনি সেটা সর্বনাশের কারণ হয়ে উঠবে।’
আমার প্রায় মনে হয়, গালিয়ানোর এই কথাগুলো থেকেই বোধ হয় বেরিয়ে আসেন অরুন্ধতী রায়ের মতো কেউ। যিনি নিজের লেখালেখি সম্পর্কে সব সময় এই সততাটুকু দেখাতে পেরেছেন। প্রচণ্ড রাজনৈতিক হওয়ার পরও রাজনীতিসর্বস্ব হয়ে থাকেননি। দারুণভাবে ভারসাম্যটুকু রক্ষা করতে পেরেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি নিজের ভেতরের সৃষ্টিশীলতাকে মরে যেতে দেননি; যা একই সঙ্গে তাকে প্রাসঙ্গিক ও সমসাময়িকও করে রেখেছে।
অরুন্ধতীর অমর সৃষ্টি ‘গড অব স্মল থিংস’ তো বটেই, সম্প্রতি দ্য গার্ডিয়ানে তার সর্বশেষ বই ‘মাদার মেরি কামস টু মি’র সম্পাদিত কিছু অংশ পড়তে পড়তেও একই ভাবনা মনে এসেছে। অভিনব বর্ণনাভঙ্গি, ভাষার কোমলতা এবং দুর্দান্ত অভিব্যক্তিই সব মিলিয়ে তার লেখাকে অনন্য এক মাত্রা দিয়েছে। মনে হয়, ছায়া বিলিয়ে রাখা দীর্ঘ এক গাছের নিচ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হেঁটে আসছি। আর এই জাদুময়তাকে আশ্রয় করে করে জীবনে ঘটে যাওয়া নির্মম ও বেদনাবিধুর অধ্যায়গুলোও একে একে বলে গেছেন তিনি। অরুন্ধতীর গদ্যে অক্ষরগুলো স্রেফ মরা কিছু চিহ্ন হয়ে পড়ে থাকে না, বরং সেগুলোর মাঝে প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে আরও ক্ষুরধার ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।
অরুন্ধতীর ফিকশন ভাবনা যে বুদ্ধিজীবীতার মোড়কে আটকে থাকেনি, বিভিন্ন সময় সে প্রমাণ তাঁর আলাপে আমরা পেয়েছি। তিনি নিজের জন্য ফিকশন লেখার আলাদা একটা পথ হয়তো বেছে নিয়েছেন। কিন্তু নিজের মতাদর্শকে তিনি অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেননি। বরং সবগুলো দুয়ার খোলা রাখার ওপরই বেশি জোর দিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে সামনে এনেছেন রাশিয়ান উপন্যাসের জটিলতা ও বৈচিত্র্যময়তাকে। তার অবস্থান উপন্যাসকে অতিসরলীকৃত ও গৃহপালিত করে রাখার বিপক্ষে। পাশাপাশি উপন্যাসকে বিভিন্ন জনরায় (রোমান্স, থ্রিলার, নাকি লিটারারি ফিকশন) ভাগ করে ভোক্তা সহায়কভাবে প্যাকেটবন্দী করার বিরুদ্ধেও তার অবস্থান। এই ভাগ করাকে তিনি মূলত উপন্যাসের পণ্যায়ন হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন।
একইভাবে ফিকশনের জগতে কীভাবে লৈঙ্গিক বৈষম্য তৈরির মধ্য দিয়ে নারীদের ‘অপর’ করা হয়, তা-ও দারুণভাবে সামনে এনেছেন অরুন্ধতী, ‘পুরুষ লেখকদের জন্য বিশাল ক্যানভাসকে সহজেই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু নারী লেখকদের ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে-চরিত্র এতগুলো কেন? এত রাজনৈতিক কেন? অথচ ‘ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিটিউড বা ওয়ার অ্যান্ড পিসে’ চরিত্র কত!’
অরুন্ধতীর মতে, আজকের অনেক তথাকথিত রুচিবান শ্রেণি, যারা সাহিত্য-সংস্কৃতির মানদণ্ড ঠিক করে, তারা আসলে সেই গভীর অস্বস্তিকর রাজনীতিকে ভয় পায়। আর এসব বিষয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ধরাও পড়ে না। অথচ আমাদের বলা হয় স্বীকৃত এক বিশ্বদৃষ্টির ভেতরেই লিখতে। এরপরও তিনি হতাশ নন। নতুন প্রজন্মের কবি-লেখকদের মধ্যে সেই ধারা ভাঙার প্রচেষ্টাকেও সাধুবাদ জানিয়েছেন। বলেছেন, সারা বিশ্ব থেকেই এখন চ্যালেঞ্জ আসছে।
আরও পড়তে পারেন-
- আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ইসলামের ভূমিকা
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যেন হুমকির মুখে না পড়ে
- সমৃদ্ধ জাতি নির্মাণে দরকার বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ ও আলেমদের এগিয়ে আসা
- সালাম-কালামের আদব-কায়দা
- বিবি খাদিজা (রাযি.): ইসলাম ধর্মের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ নারী
অরুন্ধতীর সৃষ্টিশীলতার কথা বললে আমার প্রথমেই মনে আসে চিত্রনাট্যকার ও অভিনেত্রী অরুন্ধতীর কথা। ১৯৮৫ সালে ‘ম্যাসি সাহিব’ নামের সিনেমায় অভিনয় দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু তাঁর। লিখেছেন ১৯৮৯ সালে মুক্তি পাওয়া ‘ইন হুইচ অ্যানি গিভস ইট দোজ ওয়ানস’ এবং ১৯৯২ সালের ‘ইলেকট্রিক মুন’ নামের ছবির চিত্রনাট্যও। দুটি ছবিই জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছে এবং এর মধ্যে ‘ইন হুইচ অ্যানি গিভস ইট দোজ ওয়ানস’-এর জন্য আলাদাভাবে শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকারের জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন অরুন্ধতী। এই ছবিতে অরুন্ধতীর সঙ্গে অভিনয় করেছেন শাহরুখ খান, মনোজ বাজপেয়ী ও রঘুবীর যাদবের মতো পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্র দুনিয়ায় রাজত্ব করা অভিনেতারা।
অরুন্ধতী চাইলে তো সফল এক চিত্রনাট্যকারের জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিংবা সিনেমা পরিচালনা করে বা অভিনয় করে হতে পারতেন বড় তারকা। এসব যদিও আমার ব্যক্তিগত ভাবনা। মূলত এখানেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাঁর ক্রিটিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি। ফলে তিনি নিজেকে এই মাধ্যমে সফল হিসেবে ভাবতে পারেননি। তার ভাবনা ছিল কিছুটা ভিন্ন। অরুন্ধতীর মুখেই শোনা যাক: ‘কিছু ফিল্মের সঙ্গে আমি কাজ করেছি। এগুলোকে একধরনের পাগলামি বলা যায়। কেউ ওসব ফিল্ম দেখেনি। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অংশ বলা যায় না আসলে, খুবই সামান্য অভিজ্ঞতা।’
সত্যি কথা বলতে, সিনেমার মতো একটা সামষ্টিক সৃষ্টিশীল মাধ্যমে ঠিক স্বাচ্ছন্দ্যও বোধ করছিলেন না তিনি। সিনেমার এত আয়োজন তার কাছে কঠিনই মনে হয়েছে। তবে সবচেয়ে ভুগিয়েছে কল্পনার বিষয়-আশয়কে বাস্তবে রূপ দিতে না পারার হতাশা, ‘আমার মাথায় যে সিনেমাটা ছিল, আমরা শেষ পর্যন্ত যেটা বানালাম, সেটা আলাদা হয়ে গেল। আমি চেয়েছিলাম আরও বিশৃঙ্খল একটা স্বরভঙ্গি আসুক, কিন্তু সিনেমা সম্পর্কে যথেষ্ট জানতাম না, তাই সেটা পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে পারিনি।’
যে কারণে নিজেকে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ চিত্রনাট্যকারই মনে করেছেন অরুন্ধতী, ‘আমি নিজেকে ব্যর্থ চিত্রনাট্যকার মনে করি। তবে আমি ব্যর্থতাকে সাফল্যের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিই। ব্যর্থতা আবার মানুষ করে তোলে, মাটিতে নামিয়ে আনে, জীবনের ছোট ছোট জিনিসকে আবার মূল্য দিতে শেখায়।’
‘গড অব স্মল থিংস’-এর চলচ্চিত্রায়ণ নিয়েও কঠোর অবস্থান ছিল তাঁর। ভয়ে ছিলেন, কেউ হয়তো সিনেমা বানাতে গিয়ে পুরো ছবিটাই নষ্ট করে ফেলবেন। এই ভয়েই হয়তো চলচ্চিত্রের পথে আর বেশি দূর হাঁটেননি, একাকী পথ চলাকেই করে নিয়েছেন নিজের ব্রত।
চলচ্চিত্রের বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে যে তারকাখ্যাতি মেলে, তার প্রতিও বিতৃষ্ণা ছিল তাঁর। তারকাখ্যাতিকে সরাসরি ঘৃণা করার কথা বলেছেন। এমনকি পত্রিকায় নিজের ছবি দেখলেও নাকি তার বিবমিষা জাগে। খ্যাতি নিয়ে যার এমন ভাবনা, সেলুলয়েডের চাকচিক্য তাকে কমই টানার কথা।
বলিউডের গ্লামারাস দুনিয়ায় সিনেমাকে কতটা বিনোদনের বাইরে নিতে পারবেন, তা নিয়েও সংশয় ছিল অরুন্ধতীর। শিল্পের এই মাধ্যমকে তিনি শুধুই বিনোদনের টুলস হিসেবে দেখতে চাননি। এর সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শের যে বিরোধ, তার ওপরও খানিকটা মনোযোগ টানার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে ফুলন দেবীকে নিয়ে নির্মিত শেখর কাপুরের কাল্ট ক্ল্যাসিক সিনেমা ‘ব্যান্ডিট কুইনের’ও কঠোর সমালোচনা করেছেন তিনি। বেঁচে থাকা একজন নারীর অনুমতি ব্যতীত তার ধর্ষণ দৃশ্য সিনেমায় প্রদর্শন করা যায় কি না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন অরুন্ধতী। প্রচল ভাঙা সিনেমার মর্যাদা পাওয়া ব্যান্ডিট কুইনের এই দিকটি হয়তো আলোচনাতেও আসত না, যদি অরুন্ধতী বিষয়টি সামনে না আনতেন।
সিনেমা কীভাবে বর্ণবাদ ও আধিপত্য তৈরির হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, তা নিয়েও উচ্চকণ্ঠ ছিলেন অরুন্ধতী। বিশেষ করে ভারতের অধিকাংশ নারী কালো হওয়ার পরও বলিউডের নায়িকারা কেন ফরসা, সেই অস্বস্তিকর প্রশ্ন তিনি সামনে নিয়ে এসেছিলেন। সুন্দর ও ফরসাকে সমার্থক করে দেখানোর যে প্রচেষ্টা, তাকে তীব্রভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। একই সঙ্গে বলিউডের জনপ্রিয়তা নিয়ে আতঙ্কিত বোধ করার কথাও জানান। তাঁর ভাষ্য, ‘ভয়ংকর ও অন্ধকারে মোড়া মূল্যবোধ তারা প্রচার করে। ভারতের প্রায় সবাই দরিদ্র ও দলিত। এখানকার অধিবাসীরা কালো মানুষ। বর্ণবাদ এখানে পরিষ্কারভাবে সক্রিয়।’
এই যে প্রচলের বাইরে গিয়ে দেখতে পারা, এই দৃষ্টিভঙ্গিই আলাদা করেছে অরুন্ধতীকে। এই লেখা অরুন্ধতীর সমুদ্রসম কর্মযজ্ঞের মধ্যে কয়েকটি নুড়িপাথর নিয়ে নড়াচড়া মাত্র। তার আলাপ ও দৃষ্টিভঙ্গি এতই বৈচিত্র্যময় যে একটা বই লিখেও হয়তো তা পুরোপুরি ধরা যাবে না। ফলে আমরা যখনই মানুষ, সাহস, সত্য, ক্ষমতা, সৃষ্টিশীলতা, নান্দনিকসহ ইত্যাকার বিষয় নিয়ে আলাপ করব, তখন আমাদের কোনো না কোনোভাবে অরুন্ধতীর দিকে মুখ ফেরাতে হবে। আর আমাদের এই ফিরে তাকানোই তাঁকে প্রতিনিয়ত প্রাসঙ্গিক করে রাখবে।
সংকলনে- হাসনাত শোয়েব
তথ্য ও উদ্ধৃতি সূত্র
অরুন্ধতী রায়: দানবের রূপরেখা: আলাপচারিতা, অনুবাদ: হাসান মোরশেদ
Arundhati Roy, The Art of Fiction No. 249: Interviewed by Hasan Altaf: The Paris Review
Arundhati Roy on her fugitive childhood: ÔMy knees were full of scars and cuts–a sign of my wild, imperfect, fatherless lifeÕ: The Guardian
এদুয়াযর্দো গালিয়ানোর সাক্ষাৎকার: স্কট শেরমান: অনুবাদ: সন্দীপন ভট্টাচার্য
উম্মাহ২৪ডটকম: এমএ