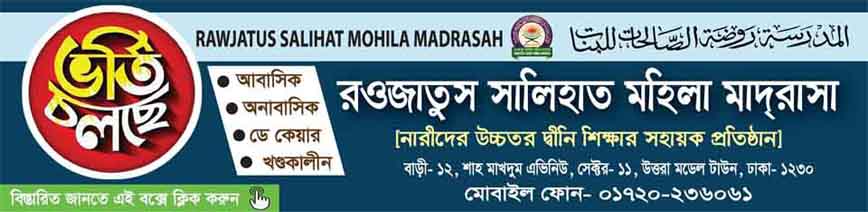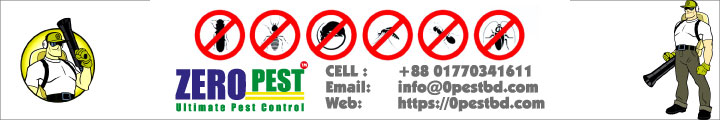দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বিজয় দিবসের এই কুচকাওয়াজে চীন প্রদর্শন করে তার অত্যাধুনিক এলওয়াই-১ এর মতো লেজার প্রতিরক্ষা। ড্রোনের ঝাঁক ঠেকাতে এটি তৈরি করা হয়েছে। ছবি: এমএসএন নিউজ
গত ৩ সেপ্টেম্বর বেইজিংয়ের তিয়ানআনমেন স্কোয়ারে ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ সামরিক কুচকাওয়াজে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এমন এক প্রতিরক্ষা কাঠামো প্রদর্শন করলেন, যা যুক্তরাষ্ট্রের মোকাবিলায় সক্ষম।
এই প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হলো—চীন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জুনিয়র পার্টনার নয়, যেমনটা গত অর্ধশতাব্দী ধরে কিছু মার্কিন নীতি-নির্ধারক ভেবেছিলেন। বরং দেশটি এখন একটি পূর্ণাঙ্গ বৈশ্বিক শক্তি, যে নিজের স্বার্থ রক্ষা ও প্রসারে প্রস্তুত।
ভারতের উপস্থিতি ও নতুন সমীকরণ
দুই দিন আগে তিয়ানজিনে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) সম্মেলনে ভারতের উপস্থিতি আরেকটি বার্তা দিয়েছে—চীন নতুন মিত্র জুটাচ্ছে, আর যুক্তরাষ্ট্র হারাচ্ছে পুরোনো বন্ধু।
একইসঙ্গে চীন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তাদের দর্শন ঘোষণা করল: বড় শক্তিগুলোর লক্ষ্য পূরণে হস্তক্ষেপ করা হবে না, যদি না তাদের দাবি করা অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি সবার জন্য সমান, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। ইউক্রেন ইস্যুতে দেখা গেছে, রাশিয়ার মতো ‘বড় শক্তির’ দৃষ্টিভঙ্গি বেইজিং- ওয়াশিংটন উভয়ের কাছেই গুরুত্ব পেয়েছে, আর অপেক্ষাকৃত দুর্বল ইউক্রেনকে সমঝোতার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।
ইতিহাস পুনর্লিখন ও আমেরিকাকে ছাপিয়ে যাওয়ার প্রয়াস
চীন আবার ইতিহাস খতিয়ে দেখছে, যা তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শিক অস্ত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের ওপর বিজয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাকে অনুচ্চারিত রাখা হয়েছে, পরিবর্তে বেইজিং থেকে বলা হচ্ছে—রাশিয়া ও চীনা কমিউনিস্ট সেনারাই জাপানকে পরাজিত করেছে।
অন্যদিকে, আমেরিকা যখন শুল্কনীতি নিয়ে অর্থনীতি পুনর্গঠনের আলোচনা করছে, সেখানে বেইজিং আঞ্চলিক উন্নয়নের অঙ্গীকার করছে—এসসিও ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের জন্য ১.৩ বিলিয়ন ডলারের তহবিল ঘোষণা করেছে। অবশ্যই এ সহায়তার মূল্য অনেক হতে পারে, কিন্তু প্রশ্ন হলো—এ মূল্য কি পশ্চিমা সহায়তার চেয়ে বেশি?
চীন সরাসরি আমেরিকার মুখোমুখি হচ্ছে না, বরং ফাঁকা জায়গাগুলো দখল করছে, এমনকি মার্কিন মিত্রদের ভেতরেও প্রভাব বিস্তার করছে। গত আট বছরে এই আত্মবিশ্বাসই চীনের কৌশলগত মনস্তাত্ত্বিক বিচ্ছিন্নতাকে দৃঢ় করেছে। ফলাফল—একটি নতুন স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা, যা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।
এশিয়ার নিরাপত্তা সমীকরণ ও আমেরিকার সংকট
ভারতের সাবেক কূটনীতিক নিরুপমা রাও যুক্তি তুলেছেন—”এশিয়ায় ভারসাম্য রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র আর ভরসাযোগ্য নয়।” এতে কোয়াড জোট—যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সমীকরণ প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।
তিনি মনে করেন, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া হয়তো নিরাপত্তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে দেবে। এর ফলে এশিয়ার নিরাপত্তা দৃশ্যপট আমূল বদলে যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের হুমকি যদি কমেও, একটি সমন্বিত এশীয় নিরাপত্তা কাঠামো তৈরি হতে পারে, যা যুক্তরাষ্ট্রনিরপেক্ষ হলেও—কার্যত চীনের বিরুদ্ধেই কাজ করবে।
আরও পড়তে পারেন-
- আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ইসলামের ভূমিকা
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যেন হুমকির মুখে না পড়ে
- সমৃদ্ধ জাতি নির্মাণে দরকার বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ ও আলেমদের এগিয়ে আসা
- সালাম-কালামের আদব-কায়দা
- বিবি খাদিজা (রাযি.): ইসলাম ধর্মের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ নারী
ইউরোপের মতো পরিস্থিতি এড়াতে চাচ্ছে এশিয়ার অনেক দেশ, যেখানে রাশিয়া ইউক্রেনে হানা দিয়ে ইইউকে অসহায় করে দিয়েছিল। এ অভিজ্ঞতা এশিয়ার দেশগুলোকে ভিন্ন কৌশল ভাবতে বাধ্য করছে।
প্রতিরক্ষা থেকে আক্রমণাত্মক কৌশলে
চীন আমেরিকার ভুলগুলো কাজে লাগাতে শিখেছে। এতদিন প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিলেও এখন আক্রমণাত্মক কৌশল ভাবছে। তবে রাজনৈতিক আক্রমণ পরিচালনায় এখনো অদক্ষ বেইজিং। অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্র যদি ভুল না করে, তবে রাশিয়া-চীনের সাফল্যের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে আসবে।
৩ সেপ্টেম্বরের কুচকাওয়াজ-পরবর্তী বার্তাই দেখাচ্ছে—চীন আর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পুনর্মিলনের আশা করে না। এখন তাদের চিন্তা নতুন এক বিশ্বব্যবস্থা গড়া, যেখানে নিয়ম-কানুন হবে পশ্চিমা মানদণ্ডের সঙ্গে তুলনার থেকে স্বাধীনতা।
ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের অস্থিরতা ও নতুন দ্বন্দ্ব
ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সি যুক্তরাষ্ট্রকে নাড়া দিয়েছে, তাঁর দ্রুত ও অস্পষ্ট সিদ্ধান্তের কারণে বৈশ্বিক অস্থিরতাও বেড়েছে। আজকের যুক্তরাষ্ট্র বলে এক, কাজ করে আরেক—ফলে অনেক দেশ চীনের দিকে তাকাচ্ছে—ত্রুটিপূর্ণ হলেও হয়তো চীনের ব্যবস্থাকেই তাদের কাছে বেশি নির্ভরযোগ্য মনে হচ্ছে।
এখানে কয়েকটি বিষয় সামনে আসছে:
১. ট্রাম্পকে শান্ত করা জরুরি। নাহলে বৈশ্বিক অস্থিরতার ফায়দা কেবল রাশিয়া ও চীনই তুলতে পারে।
২. রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের দূরত্ব স্পষ্ট করতে হবে। নইলে সন্দেহ বাড়বে, কারণ ট্রাম্পের কূটনীতির কারণে আমেরিকা কার্যত যেন পুতিনের হাতের পুতুল।
৩. অক্টোবর-নভেম্বরের ট্রাম্প-শি বৈঠক হতে চলেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে। আরেকটি বড় ব্যর্থতা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক হবে।
৪. ভারতের ভূমিকা এখনো দ্ব্যর্থক। নয়াদিল্লি – মস্কো বা বেইজিংয়ের সঙ্গে সরাসরি জোটে যাচ্ছে না – আবার আমেরিকাকেও পুরোপুরি ভরসা করছে না।
৫. জাপানের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকা এশিয়ায় অনুপস্থিত থাকলেও শূন্যতার সম্ভাবনা কম; কারণ জাপান সক্রিয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করছে।
৬. যুক্তরাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকদের চীনের বাস্তবতা বোঝার সক্ষমতায় ঘাটতি রয়েছে। কোভিড, ইউক্রেন যুদ্ধ কিংবা মধ্যপ্রাচ্য সংকটে তারা এখনো পশ্চিমা কৌশল পুরোপুরি ধরতে পারেনি।
চীন-ভারত সম্পোর্কোন্নয়নের সুবর্ণ সুযোগ
চীনের সামনে এখন এক বিরল, সুবর্ণ সুযোগ এসেছে—নিজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক নতুনভাবে গড়ে তোলার, আর সম্ভব হলে এর মাধ্যমে বিশ্বের সঙ্গেও। ভবিষ্যৎ চীন-ভারত সম্পর্কের ইঙ্গিত মেলে তিনটি ক্ষেত্রে।
১. বাণিজ্যের ক্ষেত্র
সবচেয়ে জটিল হলেও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো বাণিজ্য। ভারত চায় চীনে রপ্তানি করতে নানা ধরনের পণ্য—ওষুধ, ইলেকট্রনিকস থেকে শুরু করে উচ্চমানের ভোগ্যপণ্য। শুধু কাঁচামালের রপ্তানিকারক হতে ভারত রাজি নয়। এর বিপরীতে তারা আমদানি করতে চায় উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ।
এখানেই সংবেদনশীলতা সবচেয়ে বেশি। কারণ, এ ধরণের বিনিময় ভারতের শিল্পখাতের সক্ষমতা বাড়িয়ে—চীনের শিল্পখাতকে দুর্বল করতে পারে, বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় তাদের অবস্থানও ক্ষুণ্ণ হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে চীনের মূল সমস্যার সমাধান—অতিরিক্ত উৎপাদনের লাগাম টানা, চীনা পণ্যের জন্য ভারতের বাজার আরও উন্মুক্ত করা ও নয়াদিল্লির বৈদেশিক প্রতিযোগিতা থেকে বাজার সুরক্ষা দেওয়ার প্রবণতাকে প্রভাবিত করা।
২. ভারতের প্রতিবেশীরা
দ্বিতীয় উপাদানটি ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোকে ঘিরে। চীন দীর্ঘদিন ধরে এ দেশগুলোকে কাছে টানার চেষ্টা করছে, যেন ভারতের কূটনৈতিক পরিসরকে সীমাবদ্ধ করা যায়।
কিন্তু এর পাল্টা চালও রয়েছে। ভারত নিজেকে ঘিরে রেখেছে জাপান, ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দিয়ে—যারা সবাই চীনের উত্থান নিয়ে উদ্বিগ্ন। ফলে বেইজিং ও দিল্লির কাছে এ এক দ্বৈত ঘেরাটোপের খেলা, যা এখনো অস্থির এবং অনিশ্চিত।
৩. সীমান্ত সংকট
তৃতীয় ও তুলনামূলক সহজ বিষয় হলো– সীমান্ত। সাম্প্রতিক চুক্তি অনুযায়ী, উভয় পক্ষই সীমান্ত এলাকায় সেনা প্রত্যাহার করেছে। তবুও উত্তেজনা রয়েই গেছে। অতীতেও দিল্লি-বেইজিংয়ের মধ্যে এ ধরনের সমঝোতা হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীতে আবার সন্দেহ তৈরি হয়ে সংঘর্ষে রূপ নিয়েছে। এবার তা কতটা স্থায়ী হবে—সেটিও বড় প্রশ্ন।
@সার্বিক দৃশ্যপট
যদি আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরে চীন-ভারত সম্পর্ক সুস্থভাবে পরিচালিত হয়, আর চীন সত্যিকার অর্থে ভারতের পণ্যের বড় বাজার হয়ে ওঠে, আবার ভারতও চীনা পণ্যের বেলায় আরও উদারতা দেখায়, তবে কেবল অতিরিক্ত উৎপাদন সমস্যাই কমবে না—বরং বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে চীনের নতুন সম্পর্ক গড়ার মডেলও তৈরি হবে।
তবে মূল সমস্যা কেবল চীন-ভারত সম্পর্ক নয়—বরং চীন নিজেই। বেইজিংয়ের দরকার প্রকৃত অর্থনৈতিক সংস্কার। অদক্ষ ও অপ্রয়োজনীয় কোম্পানিগুলোকে অবসায়ন হতে দিতে হবে, যাতে বাজার খুলে যায় দক্ষ দেশীয় ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানের জন্য। এ পথ সহজ নয়, কিন্তু এটিই দেখিয়ে দেবে—চীন-ভারতের সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হবে কি না, আর চীন আদৌ বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত কি না।
সূত্র- ফ্রান্সেসকো সিসি, এশিয়া টাইমস
উম্মাহ২৪ডটকম: এমএ